সাত্যকি রায়
সম্প্রতি ভারত সরকার কর্মসংস্থান উৎসাহ দান প্রকল্প বা এমপ্লয়মেন্ট লিঙ্কড ইনসেন্টিভ (ইএলআই) প্রকল্প চালু করতে চলেছে। প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা এবং সরকার থেকে দাবি করা হয়েছে যে দু’বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাড়ে তিন কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে যার মধ্যে এক কোটি ৯২লক্ষ একেবারে নতুন কর্মপ্রার্থীর নিয়োগ হবে। মনে রাখতে হবে প্রকল্পটি সরকারি প্রকল্প কিন্তু সরকারি কাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রকল্প নয়, বরং বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প। প্রথমে যে প্রশ্নটা আসে যে যদি কর্মসংস্থান সৃষ্টিই উদ্দেশ্য হয় তাহলে ঘুর পথে না গিয়ে এই এক লক্ষ কোটি টাকা সরকারের গ্রামীণ বা শহুরে কর্মসংস্থান প্রকল্পে তো কাজে লাগানো যেত। বিশেষত এই ধরনের প্রকল্পগুলিতে যেহেতু শ্রম নিবিড় কাজের সুযোগ অনেক বেশি ফলে এই ধরনের প্রকল্পে একই টাকায় অনেক বেশি মানুষের কর্মসংস্থান করা সম্ভবপর ছিল। কিন্ত তা করা হলো না।
সরকারের নতুন প্রকল্পের দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশে বলা হচ্ছে যে কোনও বেসরকারি সংস্থায় নতুন কোনও ব্যক্তি নিযুক্ত হলে এবং ইপিএফওতে (এমপ্লয়িস প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেসন) তার নাম নথিভুক্ত হলে তার এক মাসের মাইনে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত সরকার সরাসরি ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে ওই নিযুক্ত ব্যক্তির অ্যা কাউন্টে পাঠিয়ে দেবে। এই প্রকল্পের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে যে কোনও বেসরকারি সংস্থা যদি কোন নতুন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে তবে সংস্থার মালিককেও সরকার কর্মসংস্থান ভিত্তিক অনুদান দেবে। মাসিক এক লক্ষ টাকা বেতন পর্যন্ত নিযুক্ত যে কোনও ব্যক্তির জন্য নিয়োগকারীকে মাসে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত দু’বছর ধরে দিয়ে যাবে। এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে যদি এই নতুন নিয়োগ হয়ে থাকে তবে এই অনুদান দুই থেকে চার বছর পর্যন্ত কার্যকরী হতে পারে। এই ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর উপরোক্ত অনুদান পাওয়ার একটাই পূর্ব শর্ত, তা হলো নবনিযুক্ত ব্যক্তি অন্তত ৬ মাস পর্যন্ত কাজে নিযুক্ত থাকবে। অর্থাৎ নতুন নিযুক্ত ব্যক্তি ছ’মাস কাজ করার পরই নিয়োগকারী সরকারের থেকে অনুদান পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠবে।
প্রথমত, সরকারি পয়সা খরচ করে ব্যক্তিগত নিয়োগকারীকে অনুদান দেওয়া শুধুমাত্র সরকারি কোষাগারের টাকা ব্যক্তি মালিকের পকেটে পৌঁছে দেওয়া নয় আসলে তা এই অর্থ ব্যবহারের উদ্দেশ্যকেও বদলে দেয়। সরকারি কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ টাকা ব্যবহার করা হয় সেই সমস্ত জিনিস তৈরি করতে যা মানুষের সরাসরি ব্যবহারে কাজে লাগে। স্কুল বাড়ি নির্মাণ, রাস্তার কাজ অথবা পুকুর সংস্কার এই সমস্ত কাজে যা সৃষ্টি হয় তা মানুষ সরাসরি ব্যবহার করতে পারে অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যবহার মূল্য সৃষ্টি করাটাই উক্ত বিনিয়োগের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে সরকারি অর্থ যখন ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার জন্য অনুদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন সেই অনুদান আসলে মুনাফা সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয় যা ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত সংস্থা হস্তগত করে থাকে। দ্বিতীয়ত এই প্রকল্পে আসলে লাভবান কে? নতুন নিযুক্ত কর্মচারী সরকারের কাছ থেকে একবারই পাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ ১৫০০০ টাকা। অথচ নিয়োগকারী সংস্থার মালিক দু’বছর ধরে প্রতিমাসে তিন হাজার টাকা করে পাবে অর্থাৎ মোট ৭২ হাজার টাকা এবং যদি তা কারখানা হয় তাহলে সর্বোচ্চ চার বছর পর্যন্ত ধরলে একজন কারখানার মালিকের পকেটে সরকার মোট স্থানান্তরিত করছে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, যা সে পাবে নতুন নিযুক্ত ব্যক্তির বেতন বাবদ অনুদান হিসাবে। তৃতীয়ত, মালিকের জন্য এই অনুদান দু’বছর ধরে পাওয়ার একমাত্র পূর্ব শর্ত হলো ইপিএএফও’র খাতায় এই নতুন নিয়োগ নথিভুক্ত হতে হবে। এটা ধরেই নেওয়া যায় যে এই প্রকল্প চালু হলে নথিভুক্ত তথ্য অনুযায়ী কর্মসংস্থানের পরিমাণ অনেক বেশি দেখা যাবে। কিন্তু তার মানে প্রকৃত অর্থেই নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে তা নাও হতে পারে। এর কারণ আমাদের দেশে রেগুলার কর্মসংস্থানেই মাত্র ৪২ শতাংশ শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগপত্র পেয়ে থাকে। বাকিরা কাজ করে কিন্তু তাদের খাতায়-কলমে নাম থাকে না। ক্যাজুয়াল হিসাবে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই শতাংশ আরও কম। এবার এই নাম তোলার জন্য সরকারি তথ্যে কর্মরত মানুষের অঙ্ক বেড়ে যাবে অথচ কার্যত নতুন কোনও কর্মসংস্থান নাও তৈরি হতে পারে। শুধু যার নাম নথিভুক্ত ছিল না তার নাম যোগ হয়ে যাবে। চতুর্থত, উদাহরণ স্বরূপ সরকার নির্দেশিত স্ল্যাব অনুযায়ী কোনও নতুন নিযুক্ত শ্রমিকের মাসিক মজুরি যদি ২১ হাজার টাকা হয়, তবে মালিক সেই শ্রমিককে দেবে ১৮ হাজার টাকা বাকি তিন হাজার টাকা দেবে সরকার। প্রত্যেক শ্রমিকের মজুরি বাবদ কারখানার মালিকের মাসিক দায়বদ্ধতা ২১ হাজার থেকে কমে হলো ১৮ হাজার। এর নেতিবাচক প্রভাব অসংগঠিত শ্রমজীবীদের মধ্যে পড়তে চলেছে। মালিক আসলে তার দেয় মজুরি ২১ হাজার থেকে কার্যত আঠার হাজারে নামিয়ে আনতে পারবে কারণ বলবে যে বাকিটা তো সরকার দেয়। যারা নথিভুক্ত নয় সেই শ্রমিকের জন্য সরকারি অনুদান বরাদ্দ নয় এবং মালিকও বলবে যে তার জন্য বাড়তি ৩০০০ টাকা কেন সে বহন করবে? অর্থাৎ অনথিভুক্ত শ্রমিকদের বৃহত্তর বাজারে এই প্রকল্প প্রাপ্য মজুরির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে চলেছে। সরকারি কর্মসংস্থান প্রকল্পের সঙ্গে এই ধরনের প্রকল্পের একটি বড় পার্থক্য হলো যে সরকারি প্রকল্প আসলে মজুরির নিম্নসীমাকে উপরে তুলতে পারে। মানুষের কাছে বিকল্প কাজের সংস্থান থাকলে ইচ্ছে করলেই কোনও নিয়োগকারী মজুরি কমিয়ে দিতে পারে না। এই কারণে সকলেই স্বীকার করেছিলেন যে এমএন রেগা প্রকল্প চালু হওয়ার পর গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু বেসরকারি সংস্থাকে অনুদান দেওয়ার এই ধরনের প্রকল্প যা আসলে মালিককে কর্মসংস্থানের অজুহাতে অনুদান দেয় তা কার্যত মজুরি কমিয়ে আনার কাজে ব্যবহৃত হবে। পঞ্চমত, প্রশ্ন হলো সত্যি কি এই ধরনের প্রকল্প কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করবে? মনে রাখতে হবে ব্যক্তিগত সংস্থার মালিকের কাছে উৎপাদন করার লক্ষ্য উৎপাদিত দ্রব্য নিজে ভোগ করাও নয়, আর অন্যের উপকারের জন্য সে কোন ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করছে সেটাও তার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুনাফা করা। এবং তার জন্য বাজারে যে জিনিসের চাহিদা আছে তা উৎপাদন করা এবং সেই কাজ করার জন্য শ্রমিককে নিয়োগ করার বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। এক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলো মুনাফা উপার্জনের একটি কোল্যাটেরাল বেনিফিট মাত্র। যদি কোনও মানুষকে নিয়োগ না করেই উৎপাদন ও মুনাফা করা সম্ভব হতো তাহলে মালিক স্বাভাবিকভাবে সেই পথই বেছে নিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো বাজারে যদি চাহিদার অভাব হয় তাহলে সরকার উৎপাদকের পকেটে তিন হাজার টাকা গুঁজে দিলেও কোনও উৎপাদক কি নতুন ব্যক্তিকে নিয়োগ করায় উৎসাহী হবে? যদি জিনিস বিক্রি সুনিশ্চিত না হয় তাহলে সরকার অনুদান দিলেও মালিক অতিরিক্ত ১৮হাজার টাকা গোনার ঝুঁকি নেবে কি কারণে? সরকারের খেয়াল করে দেখা উচিত যে গত প্রায় দেড় দশক ধরে ভারতবর্ষের কর্পোরেট সংস্থাগুলি বিপুল পরিমাণ মুনাফা করলেও তারা উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যথেষ্ট উৎসাহী নয়। এর কারণ এই নয় যে তাদের লোক নিয়োগ করার পয়সা নেই, আসলে লোক নিয়োগ করে যে জিনিস তারা উৎপাদন করবে তা বাজারে বিক্রি করার সমস্যা হতে পারে এই আশঙ্কাই উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির হারকে শ্লথ করে দিয়েছে। ফলে এই ধরনের উৎসাহ দান প্রকল্প আসলে কর্পোরেট সংস্থার মালিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কতটা উৎসাহিত করবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।
সাম্প্রতিক সময়ে মালিকদের উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে অনুদানের কয়েকটি প্রকল্প চালু হয়েছে। উৎপাদন করলে প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ বা পিএলআই, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলেই এলআই। এছাড়াও তাদের কর্পোরেট ট্যাক্সে ছাড় দেওয়া হয়েছে যাতে তারা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়। যদিও সরকারের আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্টই স্বীকার করেছে যে এই সমস্ত ছাড় ও অনুদান দেওয়ার পরও ব্যক্তিগত সংস্থার বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার যথেষ্ট আশাব্যাঞ্জক নয়। এছাড়াও শ্রমকোড ও অন্যান্য আইনের মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি ও প্রাপ্য অধিকার কমিয়ে আনার নানা ব্যবস্থাপনা চলছে। নয়া উদারবাদী রাষ্ট্রের মূল মন্ত্রটি হলো ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের জন্য শ্রমিক শোষণের অবাধ ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করা আবার একই সাথে সামগ্রিক পুঁজিপতি শ্রেণির পক্ষে রাষ্ট্র কিছু জনকল্যাণের ব্যবস্থা করবে যা শ্রমিকদের ন্যূনতম বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তাকে পূরণ করবে। তার জন্য ক্যাশ ট্রান্সফার বা সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পগুলো কার্যকর করা হবে। অর্থাৎ মুনাফার স্বার্থে শোষণযোগ্য শ্রমিকদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয় খরচ নিয়োগকারী পুঁজিপতির ঘাড় থেকে নামিয়ে সমাজের উপর চালান করার নানা ফন্দিফিকির চালু হচ্ছে। শোষণের উপযোগী সুস্থ সবল শ্রমিকের জোগান দেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব সমাজের! মালিক যেন প্রয়োজন মতো এই শ্রমিকদের ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা সামাজিক খরচেই সুনিশ্চিত করতে হবে। খনি থেকে যেমন কয়লা পাওয়া যাবে, গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, সরকারি পরিকাঠামোয় রাস্তাঘাট পাওয়া যাবে, এখন আবার শ্রমিকদের মজুরির অংশ ও সরকারি পয়সায় মালিকদের হাতে তুলে দিতে হবে! মনে রাখতে হবে সরকারি কোষাগার থেকে যে অনুদান দেশের মালিকদের দেওয়া হবে তার মধ্যে আপামর সাধারণ মানুষের করের টাকাও রয়েছে। শ্রমিক কৃষক নিম্নবিত্ত মানুষের দেওয়া পরোক্ষ কর ও এই সরকারি রেভিনিউয়ের অংশ। অর্থাৎ সেই টাকার অংশও যাবে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের দেয় মজুরির খরচ কমানোর কাজে। যদি এই প্রকল্পের ব্যয়ভার বহন করা হতো পুঁজিপতিদের উপর অতিরিক্ত কর চাপিয়ে তাহলে না হয় বলা যেত যে সরকার পুজিপতিদের থেকে টাকা আদায় করে সেখান থেকেই তাদের অনুদান দিচ্ছে। কিন্তু সেরকম কোনও প্রস্তাব সরকারের মাথায় নেই। অতএব মানুষের টাকা ব্যবহার করে মজুরিতে অনুদান দেওয়ার নামে আসলে পুঁজিপতিদের উৎপাদন খরচ কমানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মোটের উপর এই প্রকল্প হলো সামাজিক খরচে ব্যক্তিগত পুঁজির মুনাফার পথ আরও সুগম করে দেওয়ার ব্যবস্থা।

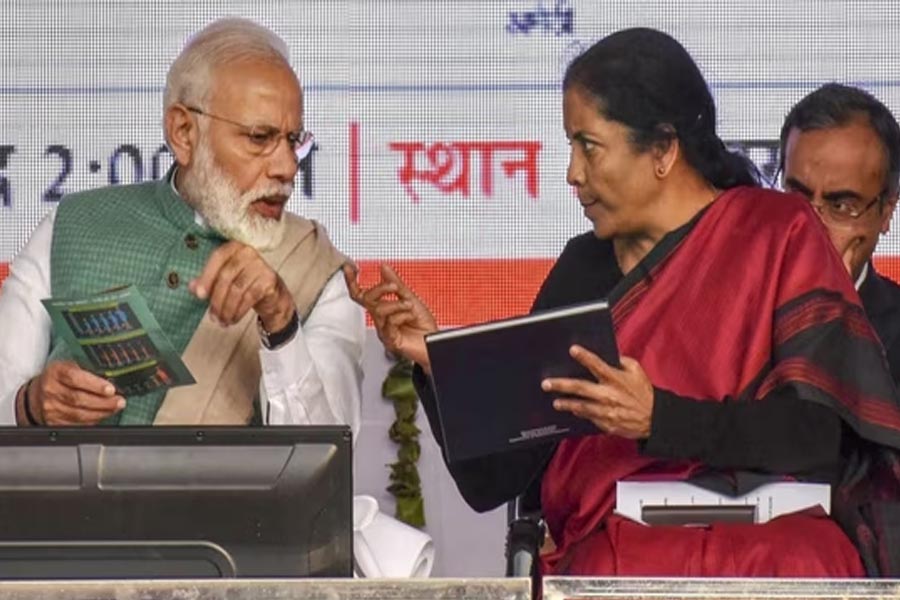



.jpeg)


Comments :0