শ্রুতিনাথ প্রহরাজ
গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তবু তাদের মেন্টর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) সর্বগ্রাসী আধিপত্য কায়েম করার লক্ষ্যে, সরকারকে পুরোদস্তুর কাজে লাগাতে মরিয়া। স্বাধীনতা উত্তরকালে এই প্রথম প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে গান্ধী হত্যা ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির কারণে অভিযুক্ত এবং সেকারণে সেই সময়ে নিষিদ্ধ হওয়া সংগঠন আরএসএস কত ভালো, তা সবিস্তারে দেশবাসীকে শুনতে হলো। আসলে এদের গুরুদক্ষিণা প্রথা চালু আছে। একসময়ের নিষ্ঠাবান সঙ্ঘ প্রচারক বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর শতবর্ষের গুরুদক্ষিণা দিলেন ঠিক এইভাবেই, সঙ্ঘ পরিবারের সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে! একই সাথে সঙ্ঘ পরিবারের পরিকল্পনা কার্যকর করতে 'জনবিন্যাস মিশন' ঘোষণা করলেন। এই মিশন আদতে দেশের মানুষের মধ্যে ধর্ম ও জাতপাত ভিত্তিক বিভেদ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে তথাকথিত 'ঘুশপেটিয়া' বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করে দেশ থেকে তাড়ানোর নামে অসহায় শরণার্থী ও সংখ্যালঘু মানুষের উপর নিপীড়ন নামিয়ে আনার সরকারি প্রচেষ্টা। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান ইত্যাদি জরুরি বিষয়গুলি আড়াল করতে কৌশল।
অথচ এই 'জনবিন্যাস মিশন' দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অসহায় মানুষের জীবনমান উন্নয়নের কথা ভেবে তৈরি হতে পারতো। কারণ, ভারতে জনবিন্যাসগত লভ্যাংশ বা সুবিধা (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) কাজে লাগানোর একটা উপযোগী পরিস্থিতি এই সময়ে তৈরি হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির পথ সুগম করা সম্ভব। জনবিন্যাসের এই লভ্যাংশ প্রাপ্তির প্রধান কারণ হলো, এদেশে জনসংখ্যায় কর্মক্ষম ব্যক্তিদের (১৫-৬৪ বছর) অনুপাত নির্ভরশীল জনসংখ্যার (শিশু এবং বয়স্কদের) তুলনায় অনেকটা বেশি। ভারতের গড় বয়স এখন প্রায় ২৮ বছর, যা উন্নয়নশীল দেশগুলির গড় বয়সের তুলনায় অনেকটাই কম। বিশেষজ্ঞদের মতে এই পরিস্থিতি তৈরি হয় দেশের জনগণের জন্ম এবং মৃত্যুহার— দুইই কম হওয়ার কারণে। অনুমান করা যায়, আগামী ২০৪১ সাল পর্যন্ত ভারত এই সুবিধা লাভ করবে।
গবেষকদের মতে, ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভারতে এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বছরে প্রায় ১.২ কোটি করে বাড়বে। এদের যদি যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হয় তাহলে দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবছর ৮৫ থেকে ৯০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কৃষি ক্ষেত্র থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমকে এভাবেই শিল্প ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এটাই ভারতবর্ষের মতো যে কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাস্তবসম্মত বোঝাপড়া হওয়া উচিত উচিত, যা নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ আর্থার লুইস তাঁর কৃষির উন্নয়ন থেকে শিল্পে রূপান্তর সংক্রান্ত গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এভাবেই দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সম্ভব। চীন বা ভিয়েতনাম এই পথেই তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে। অথচ আমাদের দেশে খোদ সরকারি তথ্য মোতাবেক, গ্রাম শহর সব মিলিয়ে গড় বেকারত্বের হার গত চার দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যা উদ্বেগজনক। আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধির এও একটি অন্যতম কারণ। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকেও আমাদের অবস্থান প্রায় তলানিতে। দু’বেলা দু’মুঠো ঠিকমতো খেতে না পাওয়া অসহায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অথচ বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট সামনে রেখে মোদী সরকার উল্লাস নৃত্য করছে, দেশে নাকি বৈষম্য-দারিদ্র অনেকটাই কমেছে! এই মুহূর্তে এদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার প্রশ্নে, এর থেকে বড় পরিহাস আর কিছু হতে পারে না।
এ কথা ঠিক ভারতের জিডিপি বাড়ছে। কিন্তু একই সাথে দেশের মানুষের আয় বৈষম্য এবং সম্পদ বণ্টনের অসমতাও ভয়ঙ্করভাবে বাড়ছে। আয় ও সম্পদ বণ্টনের সমতাহীন সমাজে আর্থিক বৈষম্যের পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্যও অনেকটাই বেড়ে যায়, যার প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী হন সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা। সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্ট নিয়ে ঠিক এভাবেই সরকারি উদ্যোগে হইচই করা হলো। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমান সময়ে ভারতে বৈষম্যের হার ক্রমহ্রাসমান হওয়ায় দারিদ্র অনেকটাই কমেছে। মানুষ ঠকানোর নিজস্ব মেকানিজমের বাইরে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের এই রিপোর্ট মোদী ও তাঁর সরকারকে অনেকটাই অক্সিজেন জুগিয়েছে সন্দেহ নেই। অথচ সরকারিভাবে এটি প্রকাশ্যে আনার সময় একবারও বলা হলো না, এই রিপোর্টের সারবত্তা নিয়ে আমাদের দেশের এবং বিশ্বের বহু অর্থনীতিবিদ ও গবেষক প্রশ্ন তুলেছেন। এ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে কারণ ভারতের প্রকৃত অর্থ সামাজিক চিত্রের সঙ্গে এই রিপোর্ট মেলে না। তাছাড়া ভারতে যেহেতু কোনও নিয়মতান্ত্রিক সম্পদ শুমারি হয় না, এ ধরনের সমীক্ষার ক্ষেত্রে সম্পদের কেন্দ্রীকরণের প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত হয় না। তাছাড়া, শুধু আয় দেখলেই তো চলে না, এদেশে সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য, ভোগের বৈষম্য, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির বৈষম্য ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় রয়েছে যার প্রকৃত পরিমাপ ছাড়া 'দেশে বৈষম্য কমেছে'— এমন মন্তব্য করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।
খুব সংক্ষেপে ভারতবর্ষের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক চিত্র একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। আগেই বলেছি ভারতের জিডিপি দেখে দেশবাসীর প্রকৃত জীবনমান অনুমান করা সম্ভব নয়। তার সবচাইতে বড় কারণ হলো এদেশের আয় ও সম্পদ বণ্টনের গুরুতর বৈষম্য। জনবিন্যাসগত লভ্যাংশ কাজে লাগানোর পূর্বশর্তই হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। অথচ, এ দেশের সার্বিক বিকাশ অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীর অন্তর্ভুক্তির সুযোগ খুবই সীমিত। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডাব্লিউ ই এফ) প্রকাশিত এই ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (আইডিআই) বা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে দেখা যাচ্ছে, উন্নয়নশীল ৭৪ টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ৬২ তম। শুধু চীন নয়, প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা নেপালও এক্ষেত্রে ভারতের থেকে এগিয়ে।
ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ডেটাবেস থেকে প্রায় একই সময়ে 'ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অসাম্য' শীর্ষক একটি সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ থমাস পিকেটি সহ আরও তিনজন অর্থনীতির গবেষক এই সমীক্ষার কাজ একত্রে পরিচালনা করেছেন। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত পর্যন্ত ভারতবর্ষে আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তারপর ধারাবাহিকভাবে এই বৈষম্য বাড়তে থাকে। গত শতাব্দীর আশির দশকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের নির্দেশে চালু হয় কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচি। এর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে, সরকারের ভূমিকা ক্রমে সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। দেশি ও বিদেশি কর্পোরেট গোষ্ঠীর মাতামাতি শুরু হয় তখন থেকেই, যা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নেয় ১৯৯১ সালে নব্য উদার অর্থনীতি চালু হওয়ার পর। এইভাবে আয় ও সম্পদের কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা বেড়েছে। মুষ্টিমেয় কিছু বিত্তশালী পরিবারের আয় ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে, যা এই দুইয়ের বণ্টনের বৈষম্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ।
অথচ, ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংশোধনীর মাধ্যমে আমাদের দেশের সংবিধানের নির্দেশিকা নীতিতে ৩৮(২) ধারা যোগ করে বলা হয়, রাষ্ট্র আয়ের বৈষম্য কমাতে এবং মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ প্রাপ্তির সুযোগের বৈষম্য দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে, কেবল ব্যক্তিদের মধ্যেই নয় বরং বিভিন্ন ক্ষেত্র বা পেশার মানুষের গোষ্ঠীর মধ্যেও একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। সংবিধানের এই সংশোধনী দেশের সমাজকল্যাণ ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নের নির্দেশ দেয়। দুঃখের হলেও একথা সত্যি, রাষ্ট্র সেই নির্দেশ কার্যকর করেনি বরং তারপর থেকেই দেশে আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। এখনতো বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবার দেশের সংবিধানের মূল মর্মবস্তুকেই মান্যতা দেওয়ার বদলে অস্বীকার করে চলেছে। তাই ওদের শাসনকালে সামাজিক ন্যায় ও মানুষের বৈষম্য মুক্তির আশা করাটাই বৃথা। ২০২২-২৩ সাল পর্যন্ত, সম্পদের এহেন সর্বাধিক কেন্দ্রীভবনের ফলে দেশে 'বিলিয়নিয়ার রাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের বিত্তশালী মানুষের উপরের দিকে থাকা মাত্র এক শতাংশ পরিবারের হাতে এদেশের জাতীয় আয়ের ২২.৬ শতাংশ এবং জাতীয় সম্পদের ৪০.১ শতাংশ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। গত দু’-আড়াই বছরে এই হার আরও বেড়েছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ভারতে এখন অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের প্রকৃত তথ্য পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। এর থেকেই বোঝা যায় বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্টে এদেশের যে বৈষম্য হ্রাসের কথা বলা হয়েছে তা কতটা হাস্যকর।
থমাস পিকেটি ও তার বন্ধুরা তাদের রিপোর্টে শুধু সমস্যা চিহ্নিত করেই কাজ শেষ করেননি। পরন্তু কিভাবে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা যায় তার পথ নির্দেশ করেছেন। তাঁদের মতে এদেশে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে, সর্বপ্রথম আয় ও সম্পদ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে কর কাঠামোর পুনর্গঠন জরুরি, যাতে সরকারি কোষাগার পুষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ও অন্যান্য মৌলিক পরিষেবায় সরকারি বিনিয়োগ অনেকটা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ শুধু আয় নয়, সম্পদের উপরও কর আরোপ করতে হবে। স্বাধীন ভারতে ১৯৫৭ সাল থেকে 'সম্পত্তি কর আইন' চালু হয়েছিল। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর কর্পোরেট গোষ্ঠীর স্বার্থ সুরক্ষায়, ২০১৬ সালে তা তুলে দেওয়া হয়। বর্তমানের এই বৈষম্য কমাতে মুষ্টিমেয় কিছু গোষ্ঠী ও পরিবারের কাছে বিশাল আকারে কেন্দ্রীভূত সম্পদকেও করের আওতায় আনা জরুরি। আয়, সম্পদ করের সঙ্গে সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে মালিকানা বজায় রাখার বন্দোবস্ত বন্ধ করার জন্য উত্তরাধিকার কর আরোপ করা দরকার। এই কাজের ফলে শুধু দেশের বিত্তশালী কিছু মানুষ বা পরিবার নয়, গড় ভারতবাসীর জীবনমান উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর জন্য দেশের ১৬৭ টি সর্বোচ্চ সম্পদশালী পরিবারের মোট সম্পদের উপর ২ শতাংশ 'সুপার ট্যাক্স' আরোপ করার কথা তাঁরা বলেছেন যা দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। কিন্তু ওঁরা বললে কি হবে, এদেশ তো এখন চলছে কর্পোরেট ও হিন্দুত্ববাদী শক্তির আঁতাতে। তাই বিত্তশালী পরিবারের ওপর সুপার ট্যাক্স চাপানোর পরিবর্তে এদেশের সরকার গত এক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে কর্পোরেট গোষ্ঠীকে শুধু ট্যাক্সের ছাড় দিয়েছে তাই নয়, ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইনের মতো নানা ফন্দি ফিকির তৈরি করে দেশের খনিজ সম্পদ, রেল, বিমানবন্দর, সমুদ্র বন্দর, বিমা, টেলি যোগাযোগ পরিকাঠামো ইত্যাদি বহু মূল্যবান সম্পদ ওদের হাতে জলের দরে তুলে দিয়েছে। আমজনতার আয় ও সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে এর প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। ফলে আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমার বদলে দেশ জুড়ে দরিদ্র অসহায় শ্রমজীবী মানুষের উপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক আক্রমণ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রতিবাদে আক্রান্ত মানুষ যাতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে না পারে তার জন্য কৃষি শ্রম সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের চালু আইন গুলির কর্পোরেটমুখী সংস্কার ঘটানো হয়েছে বা হচ্ছেও।
তাই, সরকারকে বাধ্য করতে হবে জনবিন্যাসগত সুবিধাকে কাজে লাগাতে নতুন আঙ্গিকের জনবিন্যাস মিশন গড়ে তোলার। মানুষে মানুষে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির মিশন নয়, আয় ও সম্পদের সমতা বিধান করে সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের মিশন এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভারতবাসীর এই সময়ের জরুরি অ্যা জেন্ডা হওয়া দরকার। দেশজুড়ে সেই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নতুবা, মোদীর এই বিপজ্জনক জনবিন্যাস মিশন আগামী ভারতবর্ষের জনবিন্যাসগত সুবিধাকে জনবিন্যাসগত বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে।
Highlights
সরকারকে বাধ্য করতে হবে জনবিন্যাসগত সুবিধাকে কাজে লাগাতে নতুন আঙ্গিকের জনবিন্যাস মিশন গড়ে তোলার। মানুষে মানুষে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির মিশন নয়, আয় ও সম্পদের সমতা বিধান করে সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের মিশন। এজন্য দেশজুড়ে আন্দোলন চাই। নতুবা, মোদীর এই বিপজ্জনক জনবিন্যাস মিশন ভারতের জনবিন্যাসগত সুবিধাকে জনবিন্যাসগত বিপর্যয়ে নিয়ে যাবে।

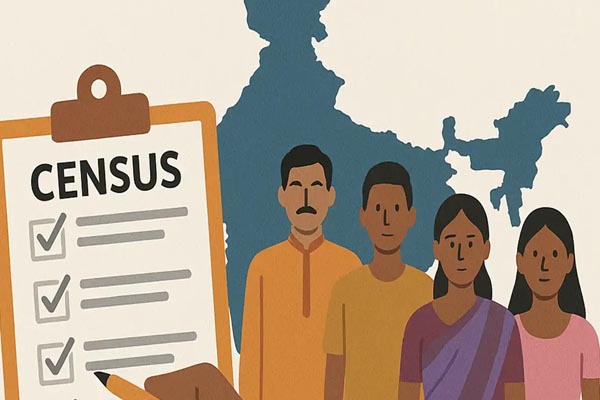






Comments :0