জিয়াদ আলী
‘Proletariat is a cultured class by nature’- Anatoly Lunacharsky.
১৯৩৫-এ কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন ‘মানুষের যে সভ্যতার রূপ আমাদের সামনে বর্তমান সে-সভ্যতা মানুষ খাদক। তার ঐশ্বর্য, তার আরাম, এমনকি তার সংস্কৃতি মাথা তোলে নিম্নতলস্থ মানুষের পিঠের ওপর চড়ে। এই নিয়েই ইউরোপে শ্রেণিবিপ্লবের লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠছে।’
দু’বছর পর ১৯৩৭-এ স্পেনে নেমে এসেছে ফ্রাঙ্কোর একনায়কতন্ত্রী সরকারের মানব-বিধ্বংসী অনাচার। তার প্রতিরোধ করতে গিয়ে স্পেনের রণাঙ্গনে প্রাণ দিতে হয়েছে বিখ্যাত লেখক বার্ডলফক্স, কর্ডওয়েল সহ গণতন্ত্র-প্রেমী লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের।
বনের পশুকে সহবত শেখালে পশুরাও হিংস্রতা ও শিকারের স্বভাব ভুলে যায়। মানুষের হত্যা প্রবৃত্তি অতো সহজে ঘোচে না। মানুষ যতো আধুনিক হয়েছে ততোই বেড়েছে তার স্বার্থপরতা, এককেন্দ্রিকতা, অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের নতুন কৌশল।
পৃথিবীর আদিম নগ্ন মানুষ সমষ্টিবদ্ধ হয়ে খাদ্য সংগ্রহ করতো। একসঙ্গে সেই খাবার খেত যে-যার মতো খিদে মেটাতে। বাড়তি খাবার মজুত করতো না একান্তভাবে নিজের জন্য। অন্যের খাবার কেড়ে খেত না। তখন মানুষ মিথ্যে বলতে শেখেনি। বঞ্চনা করতে জানতো না। গোপনীয় ব্যাভিচার, বলপূর্বক ধর্ষণও ছিল না তাদের ভিতর। তখন নারীর যৌনাঙ্গ পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পদ বা পণ্য বলে মনে করতো না কেউ-ই।
এখন মানুষ চাঁদে গিয়ে পা রেখেছে। মহাশূন্যে বিচরণ করছে যান্ত্রিক যানে চড়ে। ছুটছে সূর্যের অভিমুখে। বিজ্ঞান প্রযুক্তির এমন অভূতপূর্ব উন্নয়নের যুগে পৃথিবীর মাটিতে প্রতি দু’মিনিটে ধর্ষিত হচ্ছেন একজন নারী। প্রতি রাত্রে আধপেটা খেয়ে বা একেবারেই না খেয়ে ঘুমোতে যায় পৃথিবীর অর্ধেক শিশু। খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকে পৃথিবীর ১৫ কোটি গৃহহীন মানুষ। দলে দলে লাখো লাখো দরিদ্র মানুষ মরণের অজস্র ঝুঁকি নিয়ে নদী ও সমুদ্র পেরিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন দেশে। এ অভিযান শুধু একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই আর কয়েক টুকরো রুটির জন্য। এ কীসের সভ্যতা! এ কেমন সংস্কৃতি! মানুষকে লঙ্ঘন করে শুধু প্রতিযোগিতার অশ্ব ছোটালে শোষণ ও স্বার্থপরতার সংস্কারকে কি প্রকৃত অর্থে সংস্কৃত করে তোলা যায়। ১৯৪১-এর জুনে জার্মানির নাৎসিবাদী নেতা হিটলার পৃথিবীর প্রথম কমিউনিস্ট শাসিত দেশ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে সশস্ত্র আক্রমণ করে। সে বছর ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে তের হাজার সাতশো একাত্তর জন নিরপরাধ ইহুদিকে হত্যা করে নাৎসিরা। পুলিশ ও স্থানীয় লোকের সাহায্যেই চলে এই হত্যাকাণ্ড।
শুধু ইহুদি হবার কারণেই জার্মানির ৭০ লক্ষ নারী পুরুষ শিশু ও বৃদ্ধকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করে হিটলারের গেস্টাপো বাহিনী। নারীদের নগ্ন করে খোলা রাস্তায় ছুটতে বাধ্য করা হচ্ছে —
যারা এ দৃশ্যের বীভৎসতা থেকে আনন্দ পায় তারা কি সংস্কৃতিবান!
সভ্যতাগর্বী ইউরোপ পৃথিবীর স্বাধীন দেশের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে দখলদারি কায়েম করে মানব সভ্যতার সহজাত বিকাশকে করল শৃঙ্খলাবদ্ধ। ১৯৪১ সালে নিজের আশিতম জন্মদিনের অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সভ্যতার সঙ্কট। বললেন:
‘বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্ঘাটিত হলো একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর হতে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্রপরিচয়। ...দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মীতায়, মেকলের ভাষা প্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে, নিয়তই আলোচনা চলত শেকসপিয়রের নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয় ঘোষণায়।’
জীবনের অন্তিম সময়ে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে সর্বমানবের মুক্তির ছিটেফোঁটা চিহ্নও আর খুঁজে পাননি। তাই তিনি লিখলেন,
‘ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এতবড় প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেন বিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলেন।’ তিনি একথাও লিখলেন:
‘সমস্ত ইউরোপে বর্বরতা কিরকম নখদন্ত বিস্তার করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।’
এই কলুষ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:
‘জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।’ (সভ্যতার সঙ্কট, ১৯৪১)
রবীন্দ্রনাথ সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে মনে করতেন, সর্বমানবের মঙ্গলের কথা। নিপীড়িত সকল মানুষের অগ্রগমনের কথা। সব মানুষকে সমানভাবে জাগিয়ে তোলার কথা। ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণের সময় তিনি এসব উপলব্ধির কথাই শুনিয়েছিলেন ভারতবাসীকে।
রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের কথা ধরলে এ কথা বলতেই হবে, সংস্কৃতি মানে মননের কর্ষণ। মানুষকে অন্নময়, প্রেমময়, ভালোবাসাময় ও কর্মময় করে তোলা। মানুষের সামাজিক হয়ে ওঠা। সহমর্মী হওয়া। নতুন জীবন ও জগতের বস্তুবাদী চৈতন্যে দীক্ষিত হয়ে ওঠাতেই সাংস্কৃতিক সত্তার স্বচ্ছ রূপ সৃষ্টি হতে পারে।
মানুষকে ঈশ্বরময়, ধর্মময় করে তোলার মধ্যে সেই সাংস্কৃতিক সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। কেন না মানুষের বাস্তব অস্তিত্বই পারে মানুষের চেতনা নির্মাণ করতে।
অথচ আমাদের ধর্মশাস্ত্র ও পৌরানিক উপাখ্যানগুলোর প্রায় সবটাই ঈশ্বর ও দেবতা চর্চিত। ধর্মীয় পুরাণের কতোটা রূপক কতোটা বাস্তব তা না বুঝেই আমরা অন্ধ বিশ্বাসে তা অনুকরণ করি। আর সেসব আচার নিষ্ঠতাকে সংস্কৃতি বলে ছাপ মেরে দিই।
মহাভারতের বনপর্বে (৩১.৫) দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠীর বলছেন, ‘ধর্মের ধ্বজা তুলে নিজের সুবিধা আদায় করা হলো চরম নীতিহীনতা।’
আমরা সকলে এখন ‘ধর্মের ধ্বজা’তুলে রক্তক্ষয়ে উদ্যত। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি রক্তপাত ঘটছে ধর্মের নামে।
রবীন্দ্রনাথে শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত নৃত্যেও আধুনিক কলা চর্চার ছাপ সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সের চিত্রাঙ্কন শিল্প সৃষ্টির চেষ্টাতেও আছে সেই অভিব্যক্তি। তবু এতো সব বিজ্ঞান প্রযুক্তির উপযোগিতা ভোগ করেও সংস্কৃতি ভাবনায় আমরা নানান স্ববিরোধিতার শিকার।
সংস্কৃতি হলো আর্থিক কাঠামোর (স্ট্রাকচারের) উপরি-কাঠামো বা সুপারস্ট্রাকচার। সেই হিসাবে তা আধুনিক মননে খণ্ডিত হবার কথা। কিন্তু আমাদের একালের শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত নাটক যাত্রাপালা চলচ্চিত্রে বস্তাপচা সামন্ততান্ত্রিক ভাবনার অঢেল বিস্তার। একটা ধর্ম মিশ্রিত ‘বাবাজী’ ছাড়া আমাদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচারিত ‘সিরিয়াল’জমে না। পুজো-পার্বণের দৃশ্যায়ন সেই ধারাবাহিকে থাকতেই হবে।
আমাদের সরকারি কোনও উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য গণপতির নামে এগারো একশো ষোলটা নারকেল ভাঙা হয় একসঙ্গে। আমাদের মহান নেতারা প্রয়াত হলে কয়েক মাস ধরে তাঁর অগ্নিদগ্ধ দেহের ছাই ছড়ানো হয় নদী ও সমুদ্রের জলে। আমাদের রাষ্ট্রপতির অর্ধনগ্ন শরীরের কুম্ভমেলার স্নান-দৃশ্য সরকারি প্রচার মাধ্যমে শীর্ষ ভিজুয়াল হয়ে যায়। এ সবই হয় সরকারি ব্যয়ে, জনগণের কষ্টার্জিত রোজগার থেকে দেওয়া করের টাকায়।
১৯২৭ সালে বিখ্যাত ফরাসি ভাষার লেখক ও মনীষী রঁম্যা রঁলাকে রবীন্দ্রনাথ একটা চিঠি লেখেন। তাতে বলেন, আমাদের দেশের এথেইজম-এর বন্যা বইয়ে দেওয়া দরকার। এভাবে তিনি নাস্তিকতার প্রয়োজন অনুভব করেন। আমরা চার্বাকপন্থীদের লোকায়ত দর্শন গ্রহণ করিনি। বুদ্ধদেবের নিরীশ্বরবাদী ভাবনাকে গুলিয়ে দিয়েছি বিষ্ণুর অবতার বলে। বিষ্ণুর অবস্থান সাপের ফণীর ওপর। তাঁর সঙ্গে মাটির যোগ নেই। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর— সবই উত্তর ভারতের পার্বত্য পরিবেশ-জাত। বাঙালির এমন বড় মাপের ঈশ্বর বা দেবদেবী নেই। বাঙালি হয়ে উঠছে ক্রমশই মাটিহীন শিকড়হীন ধনহীন পরগাছা সংস্কৃতির সন্তান।
দু’ থেকে দেড় হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দ কালে রাশিয়ার উরাল পর্বত সংলগ্ন অঞ্চল থেকে পশুপালক যাযাবর আর্য ভাষার মানুষ ভারতে অনুপ্রবেশ করে পশুখাদ্য পাবার আকাঙ্ক্ষায়। ভারতের উত্তরাংশ চলে যায় সেই আর্য ভাষীদের আধিপত্যের মধ্যে। তারা ভারতের প্রাচীন কিরাত-নিষাদ নৃগোষ্ঠীর মানুষকে যুদ্ধে হারিয়ে শূদ্র ও দাস বলে ছাপ মেরে দেয়। বাঙালির রক্তে এই আর্যভাষীদের মিশ্রণ নেই। বাঙালি হলো আফ্রিকার নিগ্রো আকৃতির অস্ট্রিক ভাষী নৃগোষ্ঠীর রক্তমিশ্রিত। আমাদের পূর্বপুরুষরা আফ্রিকা থেকে ইন্দোচীনের পথ ধরে আসামের ভিতর দিয়ে সমুদ্র সংলগ্ন ভিজে স্যাঁতসেঁতে বাংলার মাটি ছুঁয়েছিল। আদতে বাংলা শব্দটাই অস্ট্রিক। বাঙালি এমনই ভিজে মাটির রসে পরিপুষ্ট। বাঙালি রসেবসে থাকতে ভালোবাসে। সেটাই তার সংস্কৃতি। তার জারি সারি ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়ার শরীরে বাতাসের কানাকানি। জল ও জমির সঙ্গে বাঙালির প্রেম-পীড়িতের সম্বন্ধ। এ নিয়েই বাঙালির বৈচিত্রময় জীবন। মিলনমুখী সংস্কৃতি।
উটকো ধর্মত্ববাদ বাঙালির সহজাত নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— ধর্ম মোহ থেকে মুক্ত হওয়ার কথা। বলেছিলেন, ‘ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো। এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।’
রামচন্দ্র, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও স্ত্রী সীতা তাঁদের বাবা ও শ্বশুর রাজা দশরথকে বলেছিলেন বড্ডো বেশি কামাসক্ত। বাঙালি ঠিক উলটো। বড্ড বেশি প্রেমাসক্ত। ষোড়শ শতকের শ্রীচৈতন্য এই প্রেমরসে সাজিয়েছিলেন একই পথে মিছিলে বামুন-চাঁড়ালকে এক সঙ্গে নিয়ে। বাঙালির সংস্কৃতি এই মহামিলনের সংস্কৃতি। সেখানে গৌড়ের নবাব সুফিবাদী হুসেন শাহও আছেন আবার হাশিম শেখ ও রমা কৈবর্তরাও আছেন। শূদ্রের ওপর জোর করে চাপানো বেগার শ্রমের সংস্কৃতি আর্যদের। বাঙালির নয়।
১৮৯৩-এর শিকাগোর ধর্মসভার ভাষণে বিবেকানন্দ মানুষের ক্ষুধার কথা বলতে ভোলেননি। তিনি বলেন ‘প্রাচ্যে ধর্মের কোনও অভাব নেই ... যা নেই তা হলো রুটি।’
বাঙালির বাস্তববোধ এ রকমই। এই বাস্তবতার টানেই রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা হয়ে ওঠেন গণদেবতা। এটাই বাঙালির সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শ।
Post Editorial
পঁচিশে বৈশাখ: সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শ

×
![]()






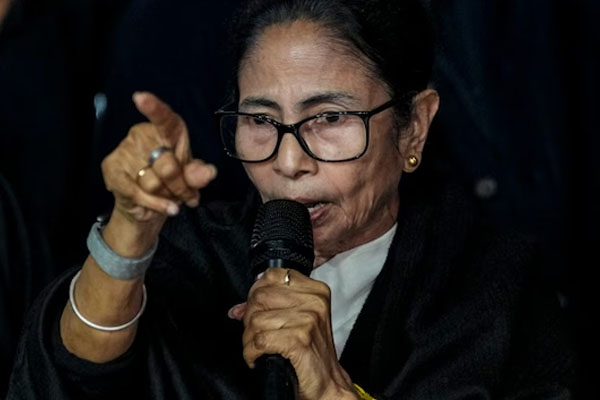
Comments :0