বইকথা — নতুনপাতা
গল্পের শৈলীতে বিজ্ঞানের কথা
অর্ণব রায়
চার্লস রবার্ট ডারউইন একেবারে অজানা কোন কথা বলেছিলেন কি? সম্ভবত না। কিন্তু তিনি জীবের বিবর্তন, অর্থাৎ জীবের শুরু এবং বিকাশের সঙ্গে, তা নিয়ে অনেকের সেযাবৎ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধারণাকে, তা অস্পষ্ট হলেও, স্পষ্টভাবে বিজ্ঞানের যুক্তিতে উন্নীত করে দিয়েছিলেন। আর, তা করেছিলেন দীর্ঘকাল ধরে অসাধারণ পরিশ্রমজাত তথ্যসংগ্রহ, সেগুলির ধৈর্যশীল পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে— অর্থাৎ পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে। জীবকুল কেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বেঁচে থাকে অথবা প্রজন্মান্তরে হারিয়ে যায়, এই মোদ্দা কথাকে তিনি যোগ্যতমের সাফল্য বলে উল্লেখ করলেন, যদিও কথাটি আদতে তাঁর নয়, দার্শনিক হার্বাট স্পেন্সারের কথা। মৌলিক যে কথাটি ডারউইন বললেন জীবের বংশধারা টিঁকে থাকার কারণ হিসাবে, তা হলো- প্রাকৃতিক নির্বাচন। প্রাথমিকভাবে বুঝতে সময় লাগল জগতের, কিন্তু যে সামান্য কয়েকজনের বোঝার তাঁরা বুঝলেন, এটি পরমশক্তি ভিত্তিক চিন্তার জগতে বিপ্লব। জীবনের উৎস ও প্রবাহের নিয়মে ধর্মাশ্রিত ধারণা প্রচলিত কোনও সর্বশক্তিমানের পরিকল্পনা ও ভূমিকাকে কোনও গুরুত্ব না দেওয়ায় এবং মানুষকে আলাদা করে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে এমন 'সারমন'কে বাতিল করার সাহসে, প্রবল আক্রমণ শুরু হলো তাঁর বিরুদ্ধে। ঠিক বিপরীতে উদ্বাহু হয়ে উঠলেন সমসাময়িক সেযাবৎ ভাবনার আরেক ভিত-ভাঙা বিপ্লবী কার্ল মার্কস স্বয়ং- জীবনগতিবিদ্যার অভিনব বিশ্লেষণ "অরিজিন অফ স্পেশিস" এর লেখক ডারউইনকে উপহার দিলেন সদ্য প্রকাশিত সমাজগতিবিদ্যার অভিনব বিশ্লেষণসমৃদ্ধ ‘ক্যাপিটাল’ বইটি, তার লেখক নিজেই।
কথিত আছে, ডারউইনের পড়ার টেবিলে নাকি পৌঁছেছিল সমসাময়িক গ্রেগর মেণ্ডেলের বংশগতির ওপর কাজের অগ্রগতির কথা, কিন্তু তিনি গুরুত্ব দেননি বা বোঝেননি। এর সত্যতা কতটা তা নিয়ে সংশয় আছে, কিন্তু এটা সত্যি, বংশগতির বাহক জিন ও তার আ্যলিলের কথা জানতে পারলে তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে অনেক বেশি পাকাপোক্ত ভিত্তি করে দিয়ে যেতে পারতেন ডারউইন নিজেই। বংশগতির সূত্র মেণ্ডেল কিছুটা দিলেন প্রায় দশ বছর ধরে তিরিশ হাজারের বেশি গাছের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, কিন্তু অপূর্ণ থাকল তাও। বহু বিজ্ঞানী ধাপে ধাপে এগোলেন, বংশগতির বাহকের চেহারাটা তারপর উন্মোচন করলেন ফ্রান্সিস ক্রিক, মরিস উইলকিন্স, জেমস ওয়াটসন। ক্রোমোজোম, ডিএনএ, জিন ক্রমশ আমাদের দৈনন্দিন শব্দরাজির মধ্যে ঢুকে পড়ল।
প্রসূন দাসের লেখা বইটি, ‘আখ্যানে বিজ্ঞান’, সম্প্রতি হাতে এল। এই প্রবন্ধ সংকলনের বইটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। বইয়ের পঞ্চাশ শতাংশ পৃষ্ঠা জুড়ে জিন তথা ডিএনএ’র কথা, কুড়ি শতাংশ জায়গা নিয়ে হোমো সেপিয়েন্সে বিবর্তন ও তার অন্য জীবকুলের প্রতি আগ্রাসনের কথা রয়েছে। বাকি জায়গায় খুব সংক্ষিপ্তভাবে অণুর গঠন, ভূতত্ত্ব, দিন-ঘন্টা সময়ের কথা, ডাইনোসোরের অবলুপ্তি, সবুজ কাছিমের রহস্য, প্রাচীনত্বের হিসাব ইত্যাদি নিয়ে নয়টি অধ্যায় রয়েছে। শিশু পাচারের প্রবন্ধটি এই সংকলনে খাপছাড়া মনে হয়। জিন ও ডিএনএ’র গঠন, মেসেঞ্জার আরএনএ, ডাবল হেলিক্স, এডনিন- গুয়ানিন- থাইমিন-সাইটোসিনের বিন্যাস, নিউক্লিক অ্যাসিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, অ্যামাইনো আ্যসিড, প্রোটিন, সাইটোপ্লাজম, কোষ বিভাজন, জিনের পরিব্যাপ্তি ইত্যাদি নিয়ে প্রাথমিক ধারণার কথা আছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানী কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে জিন গবেষণার কোন দিকে যুক্ত হয়েছেন, কিভাবে ধাপে ধাপে এগিয়েছেন তার কিছু কথা আছে। এমনকি পদার্থবিজ্ঞানীরাও কেমনভাবে যুক্ত হয়ে গেছেন প্রাণের রহস্য ডিএনএ গবেষণায় সেকথাও আলোচিত।
গল্প বলার ঢঙে লেখক বলেছেন বিজ্ঞানের কথা। তা সহজবোধ্য করেছে বিজ্ঞান রচনাগুলিকে। জিন বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়গুলিতে কৌতূহলী বালক টকাইয়ের প্রশ্ন ও তার বাবার ব্যখ্যা, মাঝেমাঝে টকাইয়ের ঠাকুর্দারও জ্ঞান ও জিজ্ঞাসার কৌশলে বিজ্ঞানকথা আলোচিত হয়েছে। মাঝেমাঝেই উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা আছে। ডিএনএ’র গঠন নিয়ে বাংলা অক্ষর ও সংখ্যা সাজিয়ে গাণিতিক চেহারা দিয়ে সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বইয়ের শেষে বর্ণানুক্রমিক সূচী পাঠককে সাহায্য করবে।
তবে, পরিশ্রমসাধ্য এই লেখা আনন্দ দিলেও কিছু অপূর্ণতার ফাঁকও রয়েছে। এমন ধরণের বই কোন বিজ্ঞান সিলেবাসের বই নয়, তাই বিজ্ঞানের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। লেখক বিজ্ঞান- চেতনার প্রয়োজনের কথা বলেছেন পরিচিতিতে, কিন্তু সামাজিক প্রেক্ষিত যুক্ত না করলে বিজ্ঞান চেতনা প্রকৃত অবয়ব পায় না। ডারউইনের আবিষ্কারের মূল অভিমুখ ও তার বিপুল প্রভাব কিছু ব্যাখ্যার দরকার ছিল বইটিতে। মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণি সামাজিক ডারউইনবাদ তৈরি করে ডারউইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে যেভাবে বিকৃত করে হাতিয়ার করেছে নিজেদের শ্রেণিশাসনের তথাকথিত ন্যায্যতা বোঝাতে - তা একটু উল্লেখ থাকলে ভালে হতো। জিনবিজ্ঞানকেও অপব্যাখ্যা করে যেভাবে ভেদাভেদের জন্য মানুষে মানুষে কৃত্রিম শ্রেষ্ঠতা ও কৃত্রিম নিকৃষ্টতাকে স্বাভাবিক বলে প্রচার করে কায়েমি স্বার্থবাদীরা— তার কথা বলা হয়নি। জিনবিজ্ঞানের বিকৃত ধারণা নাৎসী ইউনেনিক্সের উল্লেখ প্রয়োজন ছিল। বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানলেখক রিচার্ড ডকিন্সের "দ্য সেলফিস জিন" নামের অনবদ্য বিজ্ঞান বইটি পড়লে বোঝা যায় ডকিন্স জিনের স্বার্থপরতা বলতে যা বুঝিয়েছেন তা আমাদের প্রচলিত সামাজিক মানদণ্ডের স্বার্থপরতা নয়। কিন্তু বইয়ের নামটির বিকৃত ব্যাখ্যা করে উল্কার গতিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষের অনৈতিক স্বার্থপরতাকে যুক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। ডকিন্স পরে অবশ্য ব্যাখ্যা করেছেন তার এমন নাম দেওয়ার কারণ, কিন্তু বেস্টসেলার বিজ্ঞান বইটির নামকরণে তাঁর অসতর্কতার সুযোগে সেই বিকৃতির ঢেউকে তিনি পুরো ফেরাতে পারেননি। জিন নিয়ে এই বইয়ের অর্ধেক জুড়ে আলোচনায় জিনকে নিয়ে বিকৃতপ্রচারের প্রসঙ্গটিরও উল্লেখ থাকলে ভালো হতো। বিশেষত আমাদের দেশে এখন যেভাবে অপবিজ্ঞান ছদ্মবিজ্ঞান বিকৃতবিজ্ঞানকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে রাষ্ট্রমদতপুষ্ট সাম্প্রদায়িক শক্তি, সে পরিপ্রেক্ষিতে অন্ধবিশ্বাসের ও নতুন বিভ্রান্তির কুয়াশা কাটিয়ে যুক্তি ও বিজ্ঞান ভাবনাতে উৎসাহিত করতে বিজ্ঞানের সামাজিক মর্মার্থ আজ বেশি করে বলার অবকাশ রয়েছে। পাঠক তাহলে সহজে বিজ্ঞান আর সমাজের সম্পর্ককে চিহ্নিত করতে পারেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন, জিন ও বংশগতি আলোচনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রাণীকুলের যৌন নির্বাচন এবং তা কি উদ্দেশ্যে ও কিভাবে পছন্দ করা হয় এবং তার সঙ্গে জিনের সম্পর্ক— বইটিতে বলা হয়নি। জিনের আলোচনায় দু- এক জায়গায় লেখচিত্র থাকলে বুঝতে আরো সুবিধা হত। বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত পরিপ্রেক্ষিতগুলি যা বলা হয়েছে তা জিন গবেষণার ইতিহাসে আলো ফেলেছে কিছু। কিন্তু সেসবের কিছু ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র উল্লেখ করলে ভালো হতো- কারণ বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে মানুষের আগ্রহের কারণে অনেক গল্পকথা মাঝেমাঝেই আমাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।
এসব সত্ত্বেও, বইটি একটি সুখপাঠ্য বিজ্ঞানের বই। বিষয়গুলি নিয়ে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় কৌতুহলী পাঠক এই বইটিতে অবশ্যই উপাদান পাবেন।
আখ্যানে বিজ্ঞান
প্রসূন দাস। কোয়ার্ক পাবলিশার্স, ৩৩, মাধব হালদার রোড, বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৩৪। ২০০ টাকা।

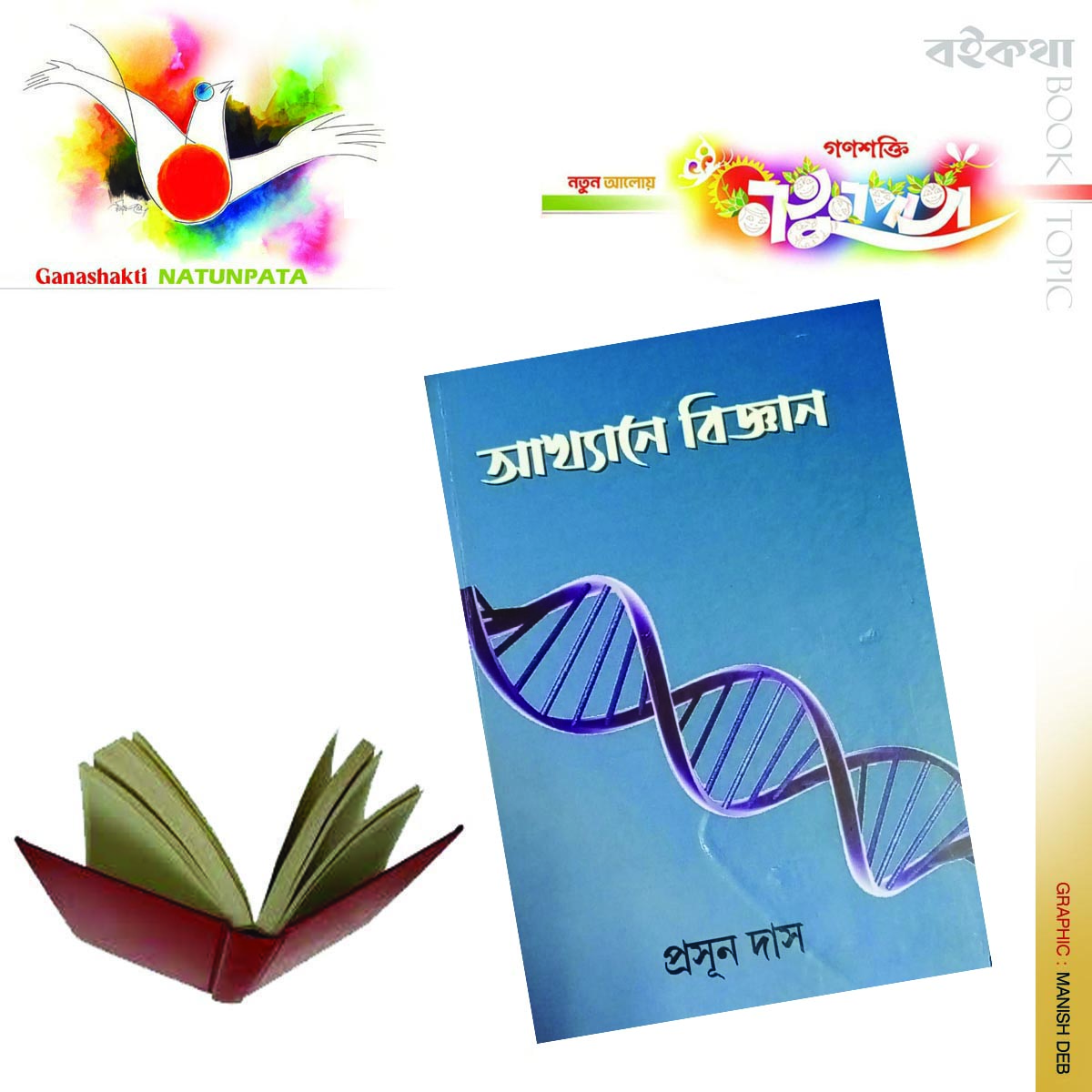
Comments :0